টিকটক,গণমাধ্যম এবং জনপরিমন্ডল
পৃথিবীতে মিডিয়া বা মাধ্যমের ধরনের অভাব নেই। এডভারটাইজিং মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া, নিউ মিডিয়া, ইন্টারেক্টিভ মিডিয়া, হাইপার মিডিয়া ইত্যাদি। এগুলো সব ঘেটে ঘেটে সংজ্ঞায়ন দেওয়া যদিও আমার মুখ্য কাজ নয় আপাতত। আমার কাজটা হলো এইটা বলে ঘটনাকে একটু বিস্তৃত করা যে, এরা প্রত্যেকে একেকটি ‘স্ট্রাকচার’ বা গঠন। যেমন ধরুন প্রিন্ট মিডিয়া নিয়েই কথা বলা যাক। কাগজ বা ক্যানভাসের সাহায্যে যোগাযোগের প্রক্রিয়াই হলো প্রিন্ট মিডিয়া। প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো প্রধানত পেপার আর ম্যাগাজিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রিন্ট মিডিয়ার চাহিদা অনেকাংশে বেড়ে গিয়েছিল জনগণের মধ্যে। আবার দেখুন ১৯৯০ এর পর থেকে টেকনোলজি ও ইন্টারনেটের বুম, ২০০১-২০০৩ সালে ইন্টারনেট ভিত্তিক কর্পোরেশন ও অনলাইন সেবা উত্থানের ফলে প্রিন্ট মিডিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে আসলো ডিজিটাল মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া। এই নতুন মিডিয়ার উত্থানের ফলে মানুষের গতিবিধি, পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ম- শৃঙ্খলে নতুনত্বের সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, পৃথিবীতে প্রতিবারই যতো ধরনের মিডিয়ার ক্লাসিফিকেশনের জন্ম হয়েছে, এরা প্রত্যেকে স্ব স্ব “স্ট্রাকচার বা গঠন”। প্রতি ক্লাসিফিকেশনের রয়েছে আলাদা আলাদা ভাষা ও গ্রামারের ব্যবহার ,বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক মনস্তত্ত্বের শ্রেণি। [যেমন যিনি পত্রিকার পাঠক, তিনি একই সাথে সোশ্যাল মিডিয়ারও পাঠক হতেও পারেন, নাও পারেন।এটি নির্ভর করে তার চিন্তা, আচার আচরণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান সময়কাল। ] মার্শাল ম্যাকলুহান এর তত্ত্ব অনুসারে , “মাধ্যমই নির্ধারণ করে মেসেজ, মেসেজ নির্ধারণ করে না।“
উক্ত আলাপটি
একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝে নেই। আমি একটা সিনেমা দেখবো। মোবাইলের ফ্রেমে দেখা সিনেমাটি
থেকে আমি যা পাবো, ল্যাপটপে সিনেমাটা দেখে আমি একটু অন্যরকম আয়েশ পাবো মোবাইলের চেয়ে।
আমেরিকার একটি গবেষণা সংস্থা এটি দেখিয়েছিলো, মোবাইল ও ল্যাপটপ ব্যবহারকারী দুইজন ব্যক্তিকে
একই সিনেমা দেখতে দেওয়া হল। দুইজনের কাছ থেকে সে সময় দুইধরনের অভিজ্ঞতা পাওয়া গিয়েছিলো।
অর্থাৎ এখানে একটা ফিলোসফিক্যাল ব্যাপারও রয়েছে, রয়েছে টেকনোলজিক্যাল ঘটনা যেটি অনেক
সময় অনেক লেখাতেই পাওয়া যায় না। আস্পেক্ট রেশিও, কালার ব্যালেন্স, ফ্রেম, উপাদান ইত্যাদি।
মোবাইলের ফ্রেম আর ল্যাপটপের ফ্রেম এর পার্থক্য আছে বলে অনেক নানন্দিক ও উপাদানগত সম্পর্ক-পার্থক্য
নির্ধারণে সুবিধা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ম্যাকলুহান সাহেবও তাই বলছিলেন ,” Medium is
the message”
আমি দুই প্যারা
দিয়ে একটু হয়তো বোঝাতে পেরেছি কেন মিডিয়ার মধ্যেও আরো আলাদা আলাদা সত্ত্বার অধিকারী
নানান ধরনের মিডিয়া(টেলিভিশন, পেপার,মোবাইল,ইত্যাদি) রয়েছে যারা বৈশিষ্ঠ্য, ধরন-নিয়ম গত জায়গা থেকে একে
অপরের চেয়ে আলাদা। আমার এই আলাপের কন্টেক্সট দেবার কারণটি হলো আসল আলাপ”স্ট্রাকচার
বা গঠন” এর আলোচনাকে একটু উন্মোচন করবো।
এই আলাপের জন্য
ডেকে আনবো কতোগুলো তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ভিত্তি যার হাত ধরে আমরা পৌছাতে পারবো কেন
স্ট্রাকচার আর মিডিয়াকে অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।এর জন্যে আমরা সাহায্য নিবো ফ্রাঙ্কফুর্ট
স্কুল অফ থটের বিখ্যাত দার্শনিক হেবারমাসের। হেবারমাসের বিখ্যাত গ্রন্থটা যারা পড়েননি
তাঁরা পড়েও দেখতে পারেন “ Structural Transformation of Public Sphere”। হেবারমাস সাহেব
বলতে চাচ্ছেন, একসময় গ্লোবাল ট্রেড এবং সামাজিক কার্যক্রম যখন শুরু হয় তখন ভিন্ন সোশ্যাল
স্ট্যাটাস ধারণকারী ব্যক্তিরা একটি আনুভূমিক সম্পর্কের মধ্যে বাস করতো, যেখানে উল্লম্ব
সম্পর্কের ক্ষেত্রে থাকতো, রাজা/বুদ্ধিজীবী/বুরোক্রেসি ইত্যাদি ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা।
ইতিহাসের এই শিফটটা শুরু হয়েছিলো ১৮৩০ ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যলুশনের পর থেকেই। ইতিহাসে
এর কারণ হিসেবে বইতে প্রধানত কয়েকটিকে দায়ী করেছে তবে এর মধ্যে দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।
একটি হলো পাবলিক ও প্রাইভেট এরিয়ার মধ্যে অত্যাধিক
ডিমারকেশন (সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সিস্টেম চালু
করার নামে ক্যাপিটালিজমের আয়তন বেড়ে যায়, ফলে পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে ফারাক)
আর দ্বিতীয়ত, মিডিয়ার ডেভেলপমেন্ট, র্যাশনালাইজেশন এবং গণতান্ত্রিকীকরণ।
আমরা যদি উক্ত দুই ধারনাকে(ক্রাইটেরিয়াকে) গ্রহন করি তাহলে আমাদের একটি কনক্লুশনকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।গণমাধ্যম যেমনঃ মোবাইলের নেটওয়ার্ক ও সোশ্যাল সিস্টেম,টেলিভিশন, মাল্টিমিডিয়ার ওপেন মার্কেটে প্রসারও বিস্তার প্রাচ্য,পাশ্চাত্য,নগর,উপনগর,মফস্বল এমনকি গ্রামের জণসাধারণের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়ে পড়ে। ফলে রাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক প্রভাব বলয় থেকে বের হয়ে বৈশ্বিক হয়ে পড়ে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া আসার ফলে স্থানীয় সীমা অতিক্রম করে সময়কে স্থান থেকে আলাদা করে দেয়। আধুনিক সমাজে ব্যক্তি একই সময়ে একই স্থানের সাথে সংযুক্ত থেকে কর্ম প্রণালী তৈরি করে এবং তা নির্মিত হতো পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে। এই আলোচনাকে যদি আমি হেবারমাসের ভাষায় একটু জোড়া লাগাতে যাই তাহলে আমি বলতে চাচ্ছি, এর পারিপার্শ্বিকতা ও কর্মপ্রণালী ও চিন্তাপদ্ধতিই আমাকে একটি স্ট্রাকচার বা গঠনের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করাতে বাধ্য করে যা বৈশ্বিক, বৈশ্বিক সংস্কৃতির বাহিরে আমি শুধুই অস্তিত্বহীন একটি সভ্যতা।
আমার আলাপ হয়তো
হালকা পাতলা বুঝে ফেলেছেন। আমরা সলে পারিপার্শ্বিকতার সাপেক্ষে বৈশ্বিক স্ট্রাকচারের
অন্তর্ভুক্ত যেখানে সংস্কৃতি বিদ্যমান। আপনারা যতোই সংস্কৃতিকে থেকে বের হন না কেন, আপনি বৈশ্বিক কালচারের
একটা অংশই নয়, আপনি আমি সেই কালচারের ইন্ডিভিজ্যূয়ালিস্ট।
হেবারমাসের
আলাপ থেকে তাহলে কি পাচ্ছি? এখন যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো সেটি হলো তার তাত্ত্বিক
পর্যালোচনাকে বর্তমান মিডীয়া এনালিসিসে আরেকটু প্রসার করা। যেমন ফেসবুক, হোয়াটস এপ,
টুইটার, টিমবার, ইন্সটাগ্রাম ইত্যাদি। যদিও আরেকটি আলাপ আছে টিকটক লাইকি নিয়ে তবে সেটা
পরে, এগুলো গবেষণামূলক আলোচনা বলে কন্টেন্ট, কালচার এবং ক্রস কালচারাল এনালিটিক্যাল
মেথডের সাহায্য লাগতে পারে এই ক্ষেত্রে। কারণ ফেসবুকের অডিয়েন্স আর টিকটকের অডিয়েন্স
এক নয়।
মূলত হেবারমাস
পরবর্তীতে যেটি বলতে চাচ্ছিলেন সেটি হলো, ইতিহাসে সমাজে আমাদের সম্পর্ক যেমন আনুভূমিক
স্তরে গঠিত ছিল, ঠিক ততোটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আর হয়নি বরং সেখানে উলটো মানুষের
র্যাশনাল চিন্তা আরো অবদমিত হওয়া শুরু করে। এর কারণ হিসেবে বলা হয় এডভারটাইজিং, প্রিন্টিং
কোম্পানি, সাংবাদিকতায় রাজকীয়তাএবং পাবলিক এফেয়ার সৃষ্টি করে মানুষের চাহিদার উপর হস্তক্ষেপ
করা ইত্যাদি। প্রোডাক্টগুলোকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যেও উক্ত বিষয়গুলো থাকার ফলে
ক্রিটিক্যাল এনালিসিস ও চোখে দেখে বাছ বিচার করার প্রক্রিয়াকে অবদমিত করে ফেলে বৈশ্বিক
কালচার।
এটা কিভাবে
সেটিরও অনেক ফিলোসফিক্যাল আলাপ রয়েছে তার মধ্যে একটা সহজ আলাপ দেই। মনে রাখবেন মিডিয়া
হলো যোগাযোগ শিক্ষার একটি অংশ। যোগাযোগ মানে এই না যে শুধুই, তথ্যের আদান প্রদান। অনেকেই
এই ভুল করে থাকে, তাদের কাছে যোগাযোগ মানে হলো তথ্য বা আদান প্রদান। যোগাযোগ মানেই
শুধু এটি নয়, এর মানে হলো প্রতীক এবং ধ্যান ধারণা প্রকাশের শিল্প।
হেবারমাসের
আলাপের এবার সংজ্ঞা ধরে টানলে একটা যৌক্তিক বিষয় খুঁজে পাওয়া সম্ভব। পাবলিক স্ফিয়ার
নিয়ে বয়ান দেবার আগেই তার মুখে উচ্চারিত হয়েছিল “in which ways public opinions
are shaped”। টিকটক হলো সেই মাধ্যম যেই মাধ্যম শেইপ সৃষ্টি করে দেয় কিভাবে জণগণের ধারণা,
অপিনিয়ন গুলো সেট আপ হবে। এই কারণে এই টিকটক থেকে ফেসবুক আমার কাছে আলাদা হয়ে গিয়েছে
এবং টিকটক বেসিস ইউজার জেনারেটেড ও ইউসিডি অপটিমাইজেশন ল্যাংগুয়েজ এই এপ্লিকেশন আমার
কাছে একটি অলটারনেটিভ মিডিয়া, যেখানে নতুন করে একটি হেবারমাসীয় বয়ানের পাবলিক স্ফিয়ারের
ট্রান্সফর্মেশন ঘটে গিয়েছে যারা ফেসবুক, টুইটার ও অন্যান্য মাধ্যমে অডিয়েন্সের চাইতেও
আলাদা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো , টিকটক আর ফেসবুক আলাদা হবার কারণ হলো টিকটক এর
কন্টেন্ট মাইক্রো ন্যারেটিভ মোডস নিয়ে গঠিত। এবং টিকটক মিডিয়ামের মধ্যে গঠিত জনপরিমন্ডল
এই কারণে হেবারমাসীয় পাবলিক স্ফিয়ার ন্যারেটিভে অন্ত্ররভুক্ত কারণ তাদের রয়েছে নিজস্ব
“পাবলিক পাওয়ার” যে পাওয়ারের সৃষ্টি হয় মিডিয়ার দ্বারা সৃষ্ট একটি কন্টেন্টে সকলের
একই মানসিকতার ফলে। পাবলিক পাওয়ার মানে গায়ের শক্তি কিংবা মেধার শক্তি নয়। এই শক্তি
বলতে বোঝানো হচ্ছেঃ- এ এক নতুন ধরনের সামাজিক সেকেন্ডারীসোসাইটি(ফেসবুক,টুইটারের বাহিরে)
যারা জীবনের গতিপ্রকৃতিতে চিন্তা ও জটিলতার বাহিরে এক র্যাডিকাল পরিমন্ডলের শুধুই
ক্রিয়েটর মাত্র (ক্ষমতার মানে যে সৃষ্টি করে পারে, প্রয়োগ নয় শুধু)।এভাবেই সে ক্ষমতায়নের
মাধ্যমে নির্জ্ঞানে চাপিয়ে রাখা ইচ্ছা, বাসনা এবং কামনাকে পূরণ করতে চায় সহজ এবং অ-জটিলতর
ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে। র্যাডিকেল বলার কারণটি হলো,তাদের দৃষ্টিকোণ মূলত লিবারেল
নয়(চুল কালার, ওয়েস্টার্ন মডেলের ড্রেস ফ্যাক্ট প্রধানত নয়) বরং নারী, সমাজ, শিক্ষা,
চলাফেরা, ভাষার ব্যবহারের যে শৃঙ্খলা ফেসবুকীয় মডেলের ইউজার জেনারেটেড মানুষের কাছ
থেকে পাওয়া যায়, টিকটকে তাকে উপস্থাপন করার কৌশল সম্পূর্ণ আবেগ-ধর্মীয়। [উল্লেখ্য যে,
ফেসবুকীয় স্ফিয়ারের মানুষের আবেগের পাশাপাশি, কগনিটিভ এবং বিহেভিওরাল সেন্স বিদ্যমান
যেখানে টিকটকীয় আলাপে অনুপস্থিত]
ভারতের টিকটক
ব্যান করার আগে রবিন পাপনেজা নামক ভদ্রলোক, যিনি থিয়েটারের নাট্যকর্মী এবং স্ট্যান্ড
আপ কমেডিয়ান, তার থেকে টিকটকের ব্যাপারে একটি মন্তব্য পাওয়া যায়, “"I don't
use Tiktok however I feel it is a revolutionary app for people from all stratas
of society to showcase their acting and comedy skills, to reach large masses of
people, without investing much and getting fame. Also, what's interesting is
that people from so called lower rungs of our society are getting
mainstream." এখানে গবেষণামূলক একটি কথাও জড়িত আছে। যখন তিনি বললেন ,” masses
of people” তখনই ক্ষমতার প্রশ্নে নতুন জনপরিমন্ডলকে এনালিসিস করতে হয়। কারণ একমাত্র
টিকটকের সুবিধা হলো, সে ফ্যান ফলোয়ার বাড়িয়ে, ফ্রি বুস্টিং করে আপনাকে ফেমাস বানাতে
পারে বলে তাঁরা মনে করে “কালচারালি স্ট্রং”। এভাবে তাঁরা সংস্কৃতির ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে
প্রবেশ করে এবং mass of people কে শুধুমাত্রই ‘নিজের আয়ত্ত্বে’ আনার কৌশল হিসেবে শিল্পের
সৃষ্টি ও আস্বাদ বাদ দিয়ে দর্শককে গাণিতিক গড়ে নিয়ে আসার কৌশল হিসেবে টিকটক একটি কার্যকরী
পদ্ধতি।
এবং কন্টেন্ট
ক্রিয়েটরদের একটি অংশ মেইনস্ট্রিমের প্রবেশ করা, তাদের টিকটকের মতো ফেসবুক-টুইটারের
অলটারনেটিভ হিসেবে ব্যবহার করার কারণও রয়েছে। বেল রোকেস নামক গবেষক দেখান যে, ৫ টি
ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিষয় গণমাধ্যম নির্ভরশীলতার সাথে সংযুক্ত-
(১)কাঠামোর
যার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়াদি গণমাধ্যমের সাথে পারস্পরিকভাবে বিজড়িত।
(২)প্রসঙ্গঃ
সামাজিক পরিবেশের প্রকৃতি
(৩) গণমাধ্যমের
ব্যবহারিক দিক
(৪) মানুষের
মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের জাল
(৫) ব্যক্তির
লক্ষ্য ও ইচ্ছা
ব্যক্তিগত মতামত
বললে আমি দাবী করবো, এ হলো সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির অন্তর্ভুক্ত যেখানে বহুস্তরভিত্তিক
প্রোডাক্ট ও কালচারের জন্ম নেয় । তবে সেগুলো মুক্তি, চিন্তা ও কর্মের লক্ষ্যে ব্যবহৃত
হয় না বরং তা নিয়োজিত হয় ভোক্তাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে এবং পূর্বনির্ধারিত প্রভাবে গ্রহীতার
চেতনাকে জড়িয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে (আমি হিরো হতে চাই/আমি ফলোয়ার বাড়িয়ে ফেমাস হতে চাই)।
ফেসবুকীয় ফলোয়ার ন্যারেটিভ টিকটকের ফলোয়ার ন্যারেটিভের চেয়ে আলাদা অনেক।
মজার ব্যাপার
হলো টিকটকের মতো এপ্লিকেশনকে সুকৌশলে অন্যান্য মিডিয়ামের পাবলিক স্ফিয়ারের বিপরীতে
দাঁড় করিয়েছে। এইজন্যেই বলছি টিকটক একটি সাংস্কৃতিক পণ্য, যে পণ্যকে সমাজের উচু-নীচ
নানা স্তরের লোকেদের জন্যে সামান্য এদিক সেদিক করে বাজারে ছাড়ার প্রক্রিয়া হিসেবেই
ব্যবহার করেছে। এভাবে যারা নির্জ্ঞানে ইচ্ছা ও বাসনাকে অবদমিত করে রেখেছে তাদের জন্য
বাজার-ক্রেতা-পণ্য-ভোক্তার প্রসেসে ঢোকা খুবই সোজা যেখানে তাঁরা এই পণ্যের শ্রেফ পরিসংখ্যানমূলক
সত্ত্বা। নিচে এক গবেষকের এন্থ্রোপলোজিক্যাল আলাপ তুলে ধরা হইলো-
এ নিয়ে বিস্তারিত অনেক প্রশ্ন আছেঃ-
১। তাহলে কোন
পদ্ধতিতে এই মানুষগুলোর মিডিয়া ট্রাস্ট সৃষ্টি হলো টিকটকের প্রতি?
২। গ্লোবাল
কালচারে হিউম্যান ইন্টারেক্টিভ মাইক্রো কালচারের হঠাত উত্থান কেন?
৩। মিডিয়া ব্যবহারের
সময় সাইকোএনালিসিস, কালচালার ও কন্টেন্ট স্টাডি তাহলে কেমন হবে?
৪। নয়া এই জনপরিমন্ডল
কেন এই মাধ্যমগুলোকে বেছে নেয়?
আরো অনেক আলাপ……………। আপাতত এতো শর্টেই প্রাইমারী আলাপ দিলাম। সেকেন্ডারী এবং ক্রিটিক্যাল আলাপ পরে।



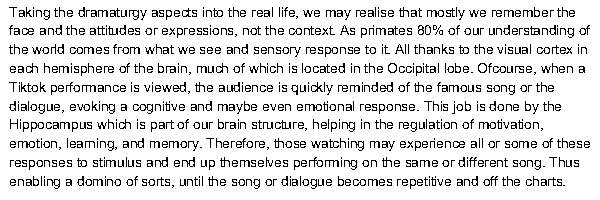


Comments
Post a Comment